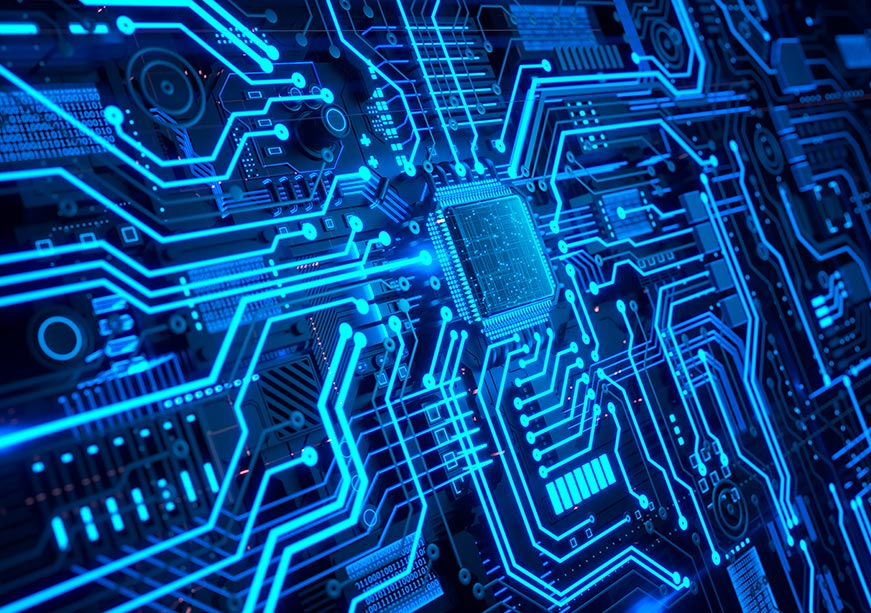২০২৪ শেষ হওয়ার পর দেশগুলির মধ্যে 'নিরাপত্তা' ও 'প্রতিরক্ষা'র ধারণাগুলি দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে বিপদের ক্ষেত্র বহুগুণ বেড়েছে, যা নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিকে পূর্ণতম মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে এবং সারা বিশ্বে নতুন পরিস্থিতি তৈরি করেছে। বিপদের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রচারের সময় হত্যার চেষ্টা, সিরিয়ায় প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের দীর্ঘদিনের সরকারের আকস্মিক পতন , হামাসের সমগ্র নেতৃত্বের উপর ইজরায়েলের প্রতারণাভিত্তিক পেজার আক্রমণ, বাল্টিক ও আফ্রিকার অ্যাটলান্টিক সমুদ্রতীরে জলের তলায় অপটিক ফাইবার কেবল সাবোতাজ করা, ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানল, বৈশ্বিক মাইক্রোসফ্ট সিস্টেমের উপর ডিস্ট্রিবিউটেড-ডিনায়াল-অফ-সার্ভিস আক্রমণ, ভারতের প্রাণবন্ত সাধারণ নির্বাচনে কথিত বিদেশী হস্তক্ষেপ , ফিলিপিনসে পরের পর ছয়টি টাইফুন আছড়ে পড়া, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের দ্রুত পতন এবং ভয়ঙ্কর মানবাধিকার লঙ্ঘন, উত্তর আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যে (ইউনাইটেড কিংডম) বেশ কয়েকটি অ-চিহ্নিত আকাশবাহী ঘটনা, এবং বিভিন্ন দেশের পরের পর হাইপারসনিক মিসাইল পরীক্ষা করা। ভারত হুমকির এই সম্পৃক্ততার কী অর্থ করবে?
একটি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কথিত প্রাক্তন অপারেটিভের একটি পডকাস্ট পর্ব ভারতে সমাদৃত হয়েছিল, যখন তিনি ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা এবং বিদেশ নীতিকে 'শক্তিশালী বাস্তববাদী' বলে অভিহিত করেছিলেন।
পডকাস্টগুলি ২০২৪ সালে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সেগুলি দীর্ঘকাল থাকবে। এক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কথিত প্রাক্তন অপারেটিভের একটি পডকাস্ট-পর্ব ভারতে সমাদৃত হয়েছিল, যেখানে তিনি ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ও বিদেশনীতিকে 'শক্তিশালীভাবে বাস্তববাদী' বলে অভিহিত করেছিলেন। এখন যেহেতু ভারতকে তার তৈরি করা ইতিবাচক ভাবমূর্তি অনুযায়ী বাঁচতে হবে, তাকে তার পথ সংশোধন অবশ্যই করতে হবে—এটি অবশ্যই বেসামরিক-সামরিক সংমিশ্রণে কাজ করবে না, কিন্তু জাতীয় নিরাপত্তা সংমিশ্রণে কাজ করবে।
আমরা অনেকেই জানি যে চিনের সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের ২০১৫ সালের প্রতিরক্ষা শ্বেতপত্র প্রথম বেসামরিক-সামরিক একীকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত কথা বলেছিল। আমরা এখন খুব ভাল করেই জানি যে বেসামরিক-সামরিক সংহতি ছিল দেং জিয়াওপিংয়ের একটি নির্মাণ, আর বেসামরিক-সামরিক সংমিশ্রণ ছিল শি জিনপিংয়ের অবদান। ২০১৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে বেশিরভাগ ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্কাররা বেসামরিক-সামরিক সংমিশ্রণে এবং বিটজিঙ্গার, কানিয়া, ও স্টোকসের ব্রিফিং সম্পর্কে ওয়াশিংটনের দেওয়া তথ্য পড়েছেন। ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ, এখন ভারতও নতুন বাস্তবতার জন্য ব্যাপকভাবে জাগ্রত: মৌলিক থিঙ্ক-ট্যাঙ্কিংয়ের কোনও বিকল্প নেই, এবং ভারতের চিনের বেসামরিক-সামরিক সংমিশ্রণকে অনুকরণ করা উচিত নয়, বরং প্রয়োজন একটি বিস্তৃত পন্থা অবলম্বন করা: জাতীয় নিরাপত্তা সংমিশ্রণ।
নিরাপত্তার স্বার্থে সামরিক ও বেসামরিক পরিসর একত্রিত করার ধারণাটি নতুন নয় এবং বাস্তবে এর কোনও চিনা উৎস নেই। ১৯৪০ সালে, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মার্কিন সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা কৌশলগুলির তথ্য সংশ্লেষণের জন্য জরুরি ব্যবস্থাপনা অফিস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। অবিলম্বে পরের বছর, ১৯৪১ সালে, একটি নতুন অফিস — বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়ন (ওএসআরডি) অফিস — প্রতিষ্ঠিত হয় যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা ও উন্নয়ন (আরঅ্যান্ডডি) আউটপুট নিরীক্ষণের জন্য । এই ওএসআরডি-ই ম্যানহাটন প্রকল্পের তত্ত্বাবধান করত। এক বছর পরে, ১৯৪২ সালে, যুদ্ধ উৎপাদন পর্ষদ তৈরি করা হয়েছিল, যার কাজ ছিল এটি নিশ্চিত করা যে বেসামরিক শিল্পগুলিকে যুদ্ধকালীন উৎপাদনের জন্য মোতায়েন করা হয়েছে এবং যুদ্ধ-প্রয়োজনীয় উপকরণগুলির একটি স্থিতিশীল সরবরাহের শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়েছে। যুদ্ধের পরে, যুদ্ধ উৎপাদন পর্ষদ বেসামরিক উৎপাদন প্রশাসনে রূপান্তরিত হয়। নতুন সত্তাটি বেশিদিন টেকেনি। ১৯৫০ সালের কোরিয়ান যুদ্ধ প্রতিরক্ষা উৎপাদন আইন নিয়ে আসে, যা প্রথমবারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংজ্ঞায়িত করেছিল একটি 'প্রতিরক্ষা শিল্প ঘাঁটি'কে, বা যাকে পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট ডোয়াইট আইজেনহাওয়ার 'সামরিক শিল্প কমপ্লেক্স' বলে অভিহিত করেছিলেন।
১৯৪০ সালে, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মার্কিন সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা কৌশলগুলির তথ্য সংশ্লেষণের জন্য জরুরি ব্যবস্থাপনা অফিস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন।
আইনটি প্রতিরক্ষা শিল্প ভিত্তি হিসাবে যা সংজ্ঞায়িত করে তা হল, "অভ্যন্তরীণ উৎস যা জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য উপকরণ বা পরিষেবা সরবরাহ করছে, বা শান্তির সময়, জাতীয় জরুরি অবস্থাকালে বা যুদ্ধের সময় সরবরাহ করবে বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করা হবে।" আইনের ১৯৫০-পরবর্তী সংশোধনীতে, আইনটি ব্যাপক জাতীয় নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলির ত্বরান্বিত উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য ঠিকাদার ও উপ-ঠিকাদার হিসাবে অবদান রাখার জন্য ছোট ব্যবসাকে সুযোগ করে দিয়েছিল। তবে সম্প্রতি চিনারা তা করার আগে পর্যন্ত একটি পরিপক্ব গণতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনও দুটি পৃথক অর্থের সঙ্গে বেসামরিক ও সামরিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেনি।
১৯৯৭ সালে যখন সিক্সটিন ক্যারেক্টর পলিসি প্রণয়ন করা হয়, তখন চিন মার্কিন 'প্রতিরক্ষা শিল্প ভিত্তি'র ধারণাটি অনুকরণ করে। সিক্সটিন ক্যারেক্টর পলিসি-তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে:
“সামরিক ও অসামরিক একত্র করা;
শান্তি ও যুদ্ধ একত্র করা;
সামরিক পণ্যকে অগ্রাধিকার;
অসামরিক যেন মিলিটারিকে সমর্থন জোগায়"
প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর অনুধাবনে, বেসামরিক-সামরিক সংমিশ্রণের লক্ষ্য হল চিনের মূল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করা, এবং উদ্ভাবনের জন্য কৌশলগত উচ্চ ক্ষেত্র দখল করতে ও বিশ্বমানের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়ে উঠতে দ্রুত এগনো, যাতে একটি প্রভাবশালী বৈশ্বিক সামরিক শক্তি হওয়ার জন্য ‘কৌশলগত সুযোগের স্বল্প সময়টিকে’ কাজে লাগানো যায়।
চিনের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের বেসামরিক ও সামরিক দুটি পৃথক অঙ্গ: 'বেসামরিক' রাষ্ট্রীয় পরিষদের অন্তর্গত আর 'সামরিক' কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশনের অন্তর্গত, এবং উভয়ই চিনের কমিউনিস্ট পার্টির শরীরের অন্তর্গত। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য, যা দুটিকেই নিয়ন্ত্রণ করে, একটি বেসামরিক-সামরিক একীকরণ বা একটি বেসামরিক-সামরিক সংমিশ্রণ অর্থবহ। যাই হোক, এটি কি গণতান্ত্রিক ভারতের জন্য ভাল কাজ করতে পারে? ভারতের সামরিক বাহিনী সরকারের ভিতরের বা বাইরের কোনও রাজনৈতিক দলের জন্য কাজ করে না, এবং ভারতও কোনও একদলীয় জাতি-রাষ্ট্র নয়। বরং, ভারত সহজাত গণতান্ত্রিক গুণাবলিসম্পন্ন একটি জাতি। তাই, আমি-সহ ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্কারদের, কখনওই এ দেশের স্বাধীন ব্যবসা ও উদ্ভাবকদের শক্তিকে কাজে লাগাতে দুর্বোধ্যভাবে চিনা-জাত শব্দগুলি ব্যবহার করা উচিত নয়। এই বিষয়ে, আমাদের অবশ্যই একটি আরও প্রাসঙ্গিক ধারণা ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে: জাতীয় নিরাপত্তা সংমিশ্রণ।
চিনের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের বেসামরিক ও সামরিক দুটি পৃথক অঙ্গ: 'বেসামরিক' রাষ্ট্রীয় পরিষদের অন্তর্গত আর 'সামরিক' কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশনের অন্তর্গত, এবং উভয়ই চিনের কমিউনিস্ট পার্টির শরীরের অন্তর্গত।
জাতীয় নিরাপত্তা সংমিশ্রণ হল, 'অনেকগুলি সিস্টেমের একটি সিস্টেম যা সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রচেষ্টা থেকে উদ্ভূত এবং বিদেশ থেকে আসা বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, প্রকৌশলী ও গাণিতিক দক্ষতাকে তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও হাতে-কলমে মসৃণভাবে একটি দুর্ভেদ্য উপায়ে একত্রিত করে ভারতবর্ষের সামগ্রিক জাতীয় নিরাপত্তার সমস্ত বিদ্যমান, উদীয়মান ও স্পর্শক ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভবপর করে।’
জাতীয় নিরাপত্তা সংমিশ্রণ হতে পারে 'ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার বিশ্বকোষীয় লক্ষ্য পূরণের জন্য সমস্ত সংস্থার — বড় বা ছোট, বেসরকারি বা অ-বেসরকারি, লাভের লক্ষ্যযুক্ত বা লাভের লক্ষ্যযুক্ত নয়, স্টার্টআপ বা কনগ্লোমারেট — থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় দার্শনিক, তাত্ত্বিক ও কার্যক্ষেত্রগত সক্ষমতা একত্র করার জন্য ভারতের সহজাত প্রয়াস’।
প্রকৃতপক্ষে, ভারতের ব্যাপক নিরাপত্তা প্রয়োজনগুলি প্রচলিত সামরিক পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নিবন্ধে আগে উল্লিখিত সাইবার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মহাকাশ, বিশেষ অভিযান, জৈব যুদ্ধ, রাসায়নিক যুদ্ধ, পরিবেশগত নিরাপত্তা, অতিমারি, গ্রহ প্রতিরক্ষা, চরম মহাকাশ আবহাওয়া, গ্রহ সুরক্ষা, পারমাণবিক-জৈবিক-রাসায়নিক (এনবিসি) ঘটনা, অর্থনৈতিক আক্রমণ, বা অপ্রত্যাশিত বিরল ঘটনাগুলি সবই সামগ্রিক জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য দেশের সরকারি-বেসরকারি উপকরণের সমন্বয় দাবি করবে। এই ধরনের সমন্বয় শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যখন দ্রুত বিকশিত জাতীয় ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা হুমকির জন্য প্রস্তুতি সমগ্র দেশের দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে বহন করা হয়। এটি শুধুমাত্র ‘জাতীয় নিরাপত্তা সংযোজন’ ধারণার মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক ভারতের পক্ষেই সম্ভব। একটি সম্পূর্ণ ভারতীয় ধারণা শুধুমাত্র ইতিবাচক আখ্যানকে শক্তিশালী করবে না, বরং ভারত যে 'শক্তিশালীভাবে বাস্তববাদী' তাও নিশ্চিত করবে।
দ্রষ্টব্য: টি এইচ আনন্দ রাও ও নীতি ঝা দ্বারা সম্পাদিত ‘বেয়ন্ড দ্য ব্লু ইয়ন্ডার: আ কিউরেটেড অ্যান্থোলজি অফ রাইটিংস অন স্পেস’ বইয়ে লেখকের অধ্যায় থেকে গৃহীত। বইটি সেন্টার ফর এয়ার পাওয়ার স্টাডিজ, নিউ দিল্লি এবং কেডব্লিউ পাবলিশার্স, নিউ দিল্লি দ্বারা প্রকাশিত।
চৈতন্য গিরি অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর নিরাপত্তা, কৌশল ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের একজন ফেলো
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.




 PREV
PREV